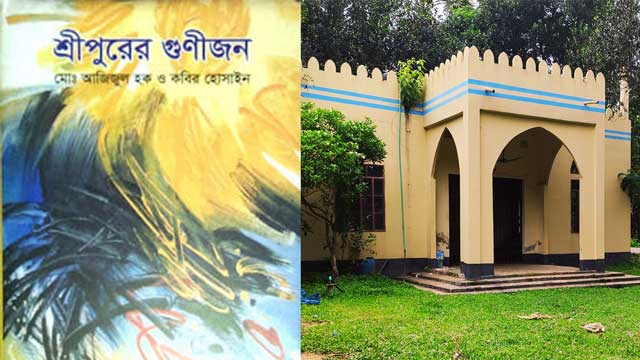বাঙালি জাতির ইতিহাস (১)
আলেকজান্ডারের সমসাময়িক গ্রীক বিবরণীতে গঙ্গার পুবদিকে গঙ্গারিড়ী বা বঙ্গ-দ্রাবিড়ী নাম এক শক্তিাশালী রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। গঙ্গা-বিধৌত এ রাজ্যের বঙ্গ-দ্রাবিড় জাতি ছিল অপরাজেয় শক্তি। টলেমী জানাচ্ছেন, গঙ্গা-মোহনার সব অঞ্চল জুড়েই গঙ্গারিড়ীরা বাস করে। তাদের রাজধানী গঙ্গা খ্যাতিসম্পন্ন এক আন্তর্জাতিক বন্দর। এখাকার তৈরি সূক্ষ্ম মসলিন ও প্রবাল-রত্ন পশ্চিম দেশে রপ্তানি হয়। তাদের মতো পরাক্রান্ত জাতি ভাতে আর নেই।
আদিতে বঙ্গ ছিল বর্তমান বাংলাদেশেরই একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল। পাল ও সেন রাজাদের আমলেও বঙ্গ সেই স্বতন্ত্র ক্ষদ্রতর রূপেই পরিচিত হয়েছে। মুসলিম শাসনের শুরুর দিকেও বাংলার শুধু পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলেই বঙ্গ নাম অভিহিত হতো। পাল ও সেন আমলে এবং মুসলিম শাসনের গোড়ার দিকে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ পরিচিত ছিল রাঢ় নামে। উত্তর বঙ্গকে বলা হতো পুন্ড্রবর্ধন, বরিন্দ্ কিংবা লাখনৌতি। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের কিচু অংশ গৌড় নামেও পরিচিত ছিল। বাংলার পুব ও দক্ষিণ অঞ্চলকে মিনহাজউদ্দীন সিরাজ তাঁর ১২৪২-৪৪ সালের তাবাকাত- ই- নাসিরীতে বঙ্গ নামে উল্লেখ করেছেন। এই এলাকা গিয়াসউদ্দীন বলবনের আমলে মুসলমানদের কাছে বাঙ্গালা নামে পরিচিত হয়। চৌদ্দ শতকের শেষভাগে জিয়াউদ্দীন বারনী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্হ তারিক-ই-ফীরুজশাহীতে প্রথম তা উল্লেখ করেন। মিনহাজের ‘বঙ্গ’ আর বারনীর ‘বাঙ্গালাহ’ বাংলার পুব-দক্ষিণবর্তী অভিন্ন অঞ্চল। বৃহত্তর ঢাকা ও সাবেক ত্রিপুরা জেলা নিয়ে গঠিত এ অঞ্চল সমতট নামেও পরিচিত হয়েছে। এ থেকে দেখা যায় যে, বর্তমান বাংলাদেশের বাইরের কোন এলাকা দূর-অতীতে কখনো বাংলা বা বাঙ্গালা কিংবা বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল না।
বাংলার স্বাধীন মুসলিম সুলতান হাজী শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ (শাসন ১৩৩৯-৫৮ ঈসায়ী) প্রথমবারের মতো গঙ্গা ও ব্রহ্মাপুত্রের নিম্ন অববাহিকার ব্যাপকতর এলাকাকে বাঙ্গালাহ নাম অভিহিত করেন। লখনৌতি (বর্তমান উত্তরবঙ্গ) ও বাঙ্গালাহকে তিনিই স্বাধীন সুলতানী শাসনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেন। সমগ্র বাংলাভাষী অঞ্চল তার আমলেই প্রথম বাঙ্গালাহ নামে পরিচিত হয় এবং তিনি প্রথমবারের মতো শাহ-ই-বাঙ্গালাহ নাম ধারণ করে নিজেকে বৃহৎ বাংলার জাতীয় শাসকরূপে ঘোষণা করেন। এর ফলে এখানে রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত ঐক্যের সূচনা হয়। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ও প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ
“ যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির দিক থেকে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, যা ছিল পাল ও সেনদের আমলে কম গৌরবের ও (কম) আদরের- সেই বঙ্গ নামেই শেষ পর্যন্ত তথাকথিত পাঠান (মুসলিম( আমলে বাংলার সমস্ত জনপদ ঐক্যবদ্ধ হল”।
(বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব- সূভাষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংক্ষেপিত, পৃষ্ঠা ২২)
এরপর বিভিন্ন সময়ে বাঙ্গালার আয়তন পরিবর্তিত হয়েছে। শুধু বৃটিশ ভারতের বৃহৎ বঙ্গ প্রদেশ নয়, পশ্চিমে বিহারের অংশ, পুবে আসাম এবং কোন কোন সময় উড়িষ্যার অংশবিশেষও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।
গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদী ও এসবের শাখানদীর প্রবাহ, বৃষ্টিপাত, মাটির পাললিক গঠন ও মৌসুমী আবহাওয়া বাংলাদেশের মাটিকে বিস্ময়করভাবে উর্বর করেছে, চাষাবাদকে করেছে উৎসাহিত। সমতল ভূমিতে বসতি স্থাপনের আকর্ষণ আর ভূ-প্রকৃতিগত কারণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দ্রুততার ফলে বাংলাদেশ হয়েছে ঘন বসতিপূর্ণ। নদ-নদীর তীর ঘেঁষে এখানে গড়ে উঠেছে মানব-বসতি, পত্তর হয়েছে গ্রাম-বন্দর। এ জনপদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, হাট-বাজার-বন্দর বিকশিত হয়েছে নদ-নদীর প্রবাহকে ঘিরে। নদ-নদীর দুই পার জুড়ে যুগ যুগ ধরে চলেছে বিরামহীন ভাঙ্গা-গড়া আর পরিবর্তনের ধরা। এদেশের অনেক জনাকীর্ণ শহর-গ্রাম-জনপদের উত্থান আর পতনের সাথে এ ধারা মিশে আছে। বাংলার জন-জীবনে এবং এদেশের রাজনৈতিক গতিপথ নিয়ন্ত্রণেও যুগ-যুগ ধরে নদ-নদীর রয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা।
নদ-নদীর প্রবাহ এ দেশের সমতলভূমিকে অসংখ্য খণ্ডে বিভাজিত করেছে। এসব ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডকে অভিন্ন রাজনৈতিক কাঠামোর আওতায় ঐক্যবদ্ধ করা ও ঐক্যবদ্ধ রাখা বরাবরই ছিল কঠিন কাজ। এসব বিচ্ছিন, বিভক্ত এলাকায় স্বাতন্ত্র্যকামী রাজনৈতিক সত্তার উত্থান ও বিকাশ এবং ক্ষুদ্র ক্ষ্রদুশাসকের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে এ এলাকার রাজনীতি চিহ্নিত হয়ে বহুকাল। রাজ্য ও প্রশাসনিক অঞ্চলের সীমানা চিহ্নিত হয়েছে নদ-নদীর প্রবাহের দ্বারা। বহিঃসীমান্তের নদীপ্রবহা এবং অভ্যন্তর ভাগের অসংখ্য শাখা, প্রবাহ, বিস্তীর্ণ জলাভূমি, দীর্ঘস্থায়ী বর্ষা ও জলপ্লাবিত সমতলভূমি এদেশকে দুর্গম করেছে। বাইরের হামলার বিরুদ্ধে দিয়েছে প্রতিরক্ষঅর প্রাকৃতিক সুবিধা। এ বিশেষ ভৌগলিক অবস্থানের কারণে আদি-বঙ্গ বরাবরই বাইরের হামলা থেকে অপেক্ষাকৃত নিরপদ ছিল। অন্যদিকে রাঢ় অঞ্চল ও উত্তর বঙ্গ প্রাচীনকালে বহুবার উত্তর ভারতীয় শাসকদের কর্তৃত্বাধীন হয়েছে।
নদী-মাতৃক বাংলাদেশের বিশেষ ভূ-প্রকৃতি এ দেশের মানুষের চরিত্র ও জীবন-দর্শনকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশ এ এলাকার মানুষকে কষ্ট-সহিষ্ণু, সাহসী ও সংগ্রামী করেছে। সংগ্রামশীল এই সাহসী মানুষেরা বেড়ে উঠেছে স্বাধীনতার দুর্জয় প্রেরণা নিয়ে। হাজার বছরের কুসংস্কার আর অধর্মেল বিকৃতি বুকে নিয়ে বৈদিক শাস্ত্র-শাসনের ভারে ন্যূব্জ ও আড়ষ্ট ভারত ধর্মে, রাষ্ট্রে বা সমাজে যে কোন পরিবর্তনের ধারাকে ভয় পায়, কিন্তু বাংলাদেশের মানুসের প্রাণ-ধর্ম ও হৃদয়-আবেগের দু’ধা স্রোতস্বিনীর মুখে সেসব জঞ্জাল ভেসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অনায়াসে।
সেমিটিক তৌহিদবাদী, ধর্মমতের উত্তর-পূরুষ এবং উন্নততর সংস্কৃতির ধারক বঙ্গ-দ্রাবিড়রা আর্যদের শির্কবাদী ধর্ম, তাদের ধর্মগ্রন্হ, তাদের তাপস্যা ও যাগযজ্ঞ এবং তাদের ব্রাহ্মণদের পবিত্র ও নরশ্রেষ্ট হওয়ার ধারণাকে কখনো কবুল করেনি, মেনে নেয়নি। রাজশক্তির প্রচণ্ড দাপট, নযিরবিহীন জুলুম-সন্ত্রাস চালিয়েও এ এলাকার সাধারণ মানুষকে বৈদিক আর্য-সংস্কৃতির বশীভূত করা যায়নি। অথচ বিশ্বাস, শিক্ষা, সৎকর্মশীলতা ও অহিংসার বাণীবাহী জৈন ধর্ম এ এলাকায় প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথেই এখানকার মানুষের চিত্ত জুড়ে গভীর আসন গেড়েছে। জীবাত্মার নির্বাণ লাভের বুদ্ধ-বাণী তাদেরকে উন্নত জীবনবোধে সঞ্জীবিত করেছে। জৈন ও বৌদ্ধ প্রচারকদের আহ্বানে এখানকার মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছে। সবশেষে মানব-মুক্তির মহাসনদ ইসলাম চিহ্নিত হয়েছে ও জনগোষ্ঠীর চূড়ান্ত মঞ্জিলরূপে।
সিন্দু নদের উপত্যকায় তার সংলগ্ন এলাকায় এবং মধ্য-ভারতে ও রাজস্থানের নানা জায়গায় প্রাক-আর্য তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন বাংলা ও তার সংলগ্ন এলাকায় এমনি সভ্যতা-সম্পন্ন এক মানবগোষ্ঠী বাস করত। তারা প্রধানত দ্রাবিড় জাতির একটি শাখা ছিল। এ উপমহাদেশে দ্রাবিড়দের আগমন ঘটেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে। তারা এসেছে সেমিটিকদের আদি বাসভূমি পশ্চিম এশিয়া থেকে। ব্যাবিলন বা মেসোপটেমিয়া দ্রাবিড়দের উৎপত্তিস্থল। এই সেমিটিকরাই পৃথিবীতে প্রথম সভ্যতার আলো ছড়িয়েছে। তারাই ইয়েমেন ও ব্যাবিলনকে সভ্যতার আদি বিকাশ ভূমিরূপে নির্মাণ করেছে। পৃথিবীতে প্রথম লিপি বা বর্ণমালা উদ্ভাবন দ্রাবিড় জাতিরই অবদান। সুপ্রাচীন এক গর্বিত সভ্যতার পতাকাবাহী এই দ্রাবিড় জাতির লোকেরা ভারতবর্ষে আর্য আগমনের হাজার হাজার বছর আগে মহোঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা সভ্যতা নির্মাণ করেছিল। অনুরূপ সভ্যতার পত্তন হয়তো তারা বাংলাদেশেও করেছিল। কিন্তু প্রাকৃতির কারণে সেগুলোর চিহ্ন এখন নেই। এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেনঃ
”তারা মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার মতো সুন্দর নগরী পাক-বাংলায় নিশ্চয়ই নির্মাণ করিয়াছিলেন। অবশ্য স্থানীয় নির্মাণ উপকরণের পার্থক্যহেতু স্থপতিতেও নিশ্চয় পাথ্যক্য ছিল। কিন্তু আজ সে সবের কোন চিহ্ন নাই। প্রাকৃতির কারণে পাক-বাংলায় চিরস্থায়ী প্রাসাদ-দুর্গ-অট্টালিকা নির্মাণের উপযোগী মাল-মশলা যেমন দুষ্প্রাপ্য, নির্মিত দালান-কোঠা ইমারত রক্ষা করাও তেমনি কঠিন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এরা নিশ্চিত শিকার। ময়নামতি, মহাস্থানগড়ের ভগ্নাবশেষ দেখিয়ে পাক-বাংলার সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও স্থপতির চমৎকারিত্ব আন্দায করা যায় মাত্র, বিচার করা যায় না”। (আমাদের কৃষ্টিক পটভূমি, পূর্বদেশ, ঈদ সংখ্যা-১৯৬৯)।
বাঙালিয় ইতিহাস-নিহার রঞ্জন রায়
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস- নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি
বঙ্গে জাতীয় ইতিহাস- ব্যোমকেশ মোস্তাফি
‘এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া’ -মাইকেল এডওয়ার্ডট
বাঙালির ইতিহাস- মোহাম্মদ হান্নান
বাঙালি জাতি বাঙালি মুসলমান ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ -সৈয়দ আবুল মকসুদ
বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস-আব্দুল করিম
আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা-মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান
বাঙালাদেশের ইতিহাস চর্চা-বদরুদ্দীন উমর
বিশ্ব ইতিহাস ও ইসলামের স্বর্ণযুগ
পর্ব ২
বাঙালি জাতির ইতিহাস( ২)
বাংলায় আর্য আগমন
দ্রাবিড় অধ্যুষিত সিন্ধু, পাঞ্জাব ও উত্তর ভারত আর্যদের দখলে চলে যাওয়ার পর এই যাযাবরদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে অধিকাংশ দ্রাবিড় দক্ষিণ ভারত, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। আর্যরা তাদের দখল বাড়াতে আরো পুবদিকে অগ্রসর হয়। সামরিক বিজয়ের সাথে সাথে বৈদিক আর্যরা তাদের ধর্ম-সংস্কৃতির বিজয় অর্জনেও সকল শক্তি নিয়োগ করে। প্রায় সম্পর্ণ উত্তর ভারত আর্যদের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু স্বাধীন মনোভাব ও নিজ কৃষ্টির গর্বে গর্বিত বঙ্গবাসীরা আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে রুকে দাঁড়ায়। ফলে করতোয়ার তীর পর্যন্ত এসে আর্যদের সামরিক অভিযান থমকে দাঁড়ায়।
আমাদের সংগ্রামী পূর্বপুরুষদের এই প্রতিরোধ-যুদ্ধ সম্পর্কে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু লিখেনঃ
“প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত যখন বিজয়ী আর্য জাতির অধীনতা স্বীকার করিয়াচিল, বঙ্গবাসীরা তখন সগর্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, আর্যদের হোমাগ্নি সরস্বতী তীর হইতে ভাগলপুরের সদানীরা (করতোয়া) নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত আসিয়া নিভিয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ সদানীরার অপর পারে অবস্থিত বঙ্গদেশের মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন নাই”। (বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা ২১)
সামরিক অভিযান ব্যাহত হওয়ার পর আর্যরা অগ্রসর হয় ঘোর পথে। তারা বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অভিযান পরিচালনা করে। তাই দেখা যায়, আর্য সামাজের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা এ দেশে প্রথম আসেনি, আগে এসেছে ব্রাহ্মণেরা। তারা এসেছে বেদান্ত দর্শন প্রচারের নামে। কেননা, ধর্ম-কৃষ্টি-সংস্কৃতি-সভ্যতার বিজয় সম্পন্ন হয়ে গেলে সামরিক বিজয় সহজেই হয়ে যাবে। এ এলাকার জনগণ ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম পরিচালনা করেন, তা ছিল মূলত তাদের ধর্ম-কৃষ্টি-সভ্যতা হেফাযত করার লড়াই। তাদের এই প্রতিরোধ সংগ্রাম শত শত বছর স্থায়ী হয়। ‘স্বর্গ রাজ্যে’ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে দীর্ঘকাল দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংগ্রামের যে অসংখ্য কাহিনী ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ প্রভৃতি আর্য সাহিত্যে ছড়িযে আছে, সেগুলো আসলে আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিরোধ ও মুক্তি সংগ্রামেরই কাহিনী। আমাদের পূর্ব পুরুষদের গৌরবদীপ্ত সংগ্রামের কাহিনীকে এসব আর্য সাহিত্যে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোন জাতির ধর্মশাস্ত্রে কোন মানবগোষ্ঠীকে এমন নোংরা ভাষায় চিহ্নিত করার নযীর পাওয়া যাবে না। উইলিয়াম হান্টার তার ‘এ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল’ বইয়ে ও প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ
“সংস্কৃত সাহিত্যে বিবৃত প্রথম ঐতিহাসিক ঘটনা হলো আদিম অধিবাসীদের সাথে আর্যদের বিরোধ। এই বিরোধজনিত আবেগ সমানভাবে ছড়িয়ে রয়েছে ঋষিদের স্তবগানে, ধর্মগুরুদের অনুশাসনে এবং মহাকবিদের কিংবদন্তীতে। ……… যুগ যুগ ধরে সংস্কৃত প্রবক্তারা আদিবাসীদেরকে প্রতিটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার হতে বঞ্চিত করে তাদের থেকে ঘৃণাভরে দূরে থেকেছে”।
সাংস্কৃতিক সংঘাত
কামরুদ্দীন আহমদ তাঁর ‘এর সোশ্যাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল’ বইয়ে দেখিয়েছেনঃ তিন স্তরে বিভক্ত আর্য সমাজের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা প্রথমে বাংলায় আসেনি। এদেশে প্রথমে এসেছে ব্রহ্মণেরা। তারা এসেছে বেদান্ত দর্শন প্রচারের নামে। বাংলা ও বিহারের জনগণ আর্য-অধিকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন পরিচালনা করেন, তাও ছিল ধর্মভিত্তিক তথা সাংস্কৃতিক।
আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ধর্ম তথা সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে জেগে ওঠা এই এলাকার সেমিটিক ঐতিহ্যের অধিকারী জনগণের সংক্ষোভের তোড়ে উত্তরাপথের পূর্বপ্রান্তবর্তী প্রদেশগুলোর আর্য রাজত্ব ভেসে গিয়েছিল।
বঙ্গ-দ্রাবিড়দের প্রতিরোধের ফলে অন্তত খ্রিস্টপূর্ব চার শতক পর্যন্ত এদেশে আর্য-প্রভাব রুখে দেওয়া সম্ভব হয়। খ্রিস্টপূর্ব চার শতকে মৌর্য এবং তার পর গুপ্ত রাজবাংশ প্রতিষ্ঠার আগে বাংলায় আর্য ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়নি। মৌর্যদের বিজয়কাল থেকেই বাংলাদেশে আর্য প্রভাব বাড়তে থাকে। তারপর চার ও পাঁচ খ্রিস্টাব্দের গুপ্ত শাসনামলে আর্য ধম, আর্য ভাষা ও আর্য সংস্কৃতি বাংলাদেশে প্রত্যক্ষভাবে শিকড় গাড়ে।
মৌর্য বংশের শাসনকাল পর্যন্ত বৌদ্ধ-ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। আশোকের যুগ পর্যন্ত এই ধর্মে মূর্তির প্রচলন ছিল না। কিন্তু তারপর তথাকথিত সমন্বয়ের নামে বৌদ্ধ ধর্মে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু তান্ত্রিকতার প্রবেশ ঘটে। হিন্দু দেব-দেবীরা বৌদ্ধ মূর্তির রূপ ধারণ করে বৌদ্ধদের পূজা লাভ করতে শুরু করে। বৌদ্ধ ধর্মের এই বিকৃতি সম্পর্কে মাইকেল এডওয়ার্ডট ‘এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া’ বইয়ে লিখেছেনঃ
“Buddhism had, for a variety of reasons, declined and many of its ideas and forms had been absorbed into Hinduism. The Hinduization of the simple teachings of Gautama was reflected in the elevation of th Buddha into a Divine being surrounded, in sculptural representations, by the gods of the Hindu partheon. The Buddha later came to be shown as an incarnation of Vishnu.”
সতিশচন্দ্র মিত্র তাঁর ‘যশোর খুলনার ইতিহাস’ গ্রন্হে লিখেছেনঃ
“যোগীরা এখন হিন্দুর মত শবদেহ পোড়াইয়া থাকেন, পূর্বে ইহা পুঁতিয়া রাখিতেন। …….. উপবিষ্ট অবস্থায় পুঁতিয়া রাখা হিন্দুদের চোখে বিসদৃশ লাগিত, তাঁহারা মনে করিতেন, উহাতে যেন শবদেহ কষ্ট পায়”।
অর্থাৎ হিন্দুদের চোখে বিসদৃশ লাগার কারণে এভাবে বৌদ্ধদেরকে পর্যায়ক্রমে তাদের ধর্ম-সংস্কৃতি তথা জীবনাচরণের অনেক বৈশিষ্ট্যই মুছে ফেলতে হয়েছিল। অশোকের সময় পর্যন্ত বুদ্ধের প্রতিমা-পূজা চালু ছিল না। পরে বুদ্ধের শূন্য আসনে শোভা পেল নিলোফার বা পদ্ম ফুল। তারপর বুদ্ধের চরণ দেখা গেল। শেষে বুদ্ধের গোটা দেহটাই পূজার মণ্ডপে জেঁকে বসল। এভাবে ধীরে ধীরে এমন সময় আসল, যখন বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দু ধর্ম থেকে আলাদা করে দেখার সুযোগ লোপ পেতে থাকল।
গুপ্ত আমলে বাংলাদেশে আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দোর্দন্ড প্রতাপ শুরু হয়। আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির স্রোত প্রবল আছড়ে পড়ে এখানে। এর মোকাবিলায় জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিচালিত হয় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকে আশ্রয় করে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি বাংলা ও বিহারের জনগণের আত্মরক্ষার সংগ্রামে এ সময় প্রধান ভূমিকা পালন করে। আর জনগণের আর্য-আগ্রাসনবিরোধী প্রতিরোধ শক্তিকে অবলম্বন করেই বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি দীর্ঘদিন এ এলাকার প্রধান ধর্ম ও সংস্কৃতিরূপে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের মতে ঐতিহাসিকও স্বীকার করেছেনঃ
“আর্যরাজগণের অধঃপতনের পূর্বে উত্তরাপথের পূর্বাঞ্চলে আর্য ধর্মের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন উপি্থি হইয়াছিল। জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম এই আন্দোলনের ফলাফল”।(বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৭-২৮)
এ আন্দোলনের তোড়ে বাংলা ও বিহারে আর্য রাজত্ব ভেসে গিয়েছিল। আর্য-দখল থেকে এ সময় উত্তরাপথের পুব-সীমানার রাজ্যগুলো শুধু মুক্তই হয়নি, শতদ্র নদী পর্যন্ত সমস্ত এলাকা অনার্য রাজাদরে অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম ও সংস্কৃতির অনাচারের বিরুদ্ধে সমুত্থিত জনজাগরণের শক্তিতেই শিশুনাগবাংশীয় মহানন্দের শূদ্র-পুত্র মাহপদ্মনন্দ ভারত-ভূমিকে নিঃক্ষত্রিয় করার শপথ নিয়েছিলেন এবং ক্ষত্রিয় রাজকুল নির্মূল করে সমগ্র আর্যবার্ত অনার্য অধিকারে এনে ‘একরাট’ উপাধি ধারণ করেছিলেন।
বাংলাদেশেই আর্যবিরোধী সংগ্রাম সবচে প্রবল হয়েছিল। এর কারণ হিসেবে আবদুল মান্নান তালিব লিখিছেনঃ
“সেমিটিক ধর্ম অনুসারীদের উত্তর পুরুষ হিসেবে এ এলাকার মানুষের তৌহিদবাদ ও আসমানী কিতাব সম্পর্কে ধারণা থাকাই স্বাভাবিক এবং সম্ভাবত তাদের একটি অংশ আর্য আগমনকালে তৌহীদবাদের সাথে জাড়িত ছিল। এ কারণেই শের্কবাদী ও পৌত্তলিক আর্যদের সাথে তাদের বিরোধ চলতে থাকে”। (বাংলাদেশে ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩৪)
জৈন ধর্মের প্রচারক মহাবীর আর বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক গৌতমের জীবনধারা এবং তাদের সত্য-সন্ধানের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে মওলানা আবুল কালাম আযাদসহ অনেক গবেষক মনে করেন যে, তারা হয়তো বিশুদ্ধ সত্য ধর্মই প্রচার করেছেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র ও বিকৃতি তাদের সে সত্য ধর্মকে পৃথিবীর বুক থেকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে যে, তার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া আজ অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে মান্নান তালিব লিখেছেনঃ
“জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলে এ ষড়যন্ত্রের বহু ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। এ উভয় ধর্মই আর্যদের ধর্মীয় গ্রন্হ বেদকে ঐশী গ্রন্হ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। তপস্যা, যাগযজ্ঞ ও পশুবলিকে অর্থহীন গণ্য করে। ব্রাহ্মণদের পবিত্রাত্মা ও নরশ্রেষ্ঠ হওয়ার ধারণাকে সমাজ থেকে নির্মূল করে দেয়। ফলে বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি নড়ে উঠে। স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণ এ ধর্মদ্বয়ের আহ্বানে বিপুলভাবে সাড়া দেয়। দ্রাবিড় ও অন্যান্য অনার্য ছাড়া বিপুল সংখ্যক আর্যও এ ধর্ম গ্রহণ করে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মদ্বয়কে প্রথমে নাস্তিক্যবাদের অন্তর্ভুক্ত করে। নাস্তিক্যবাদের সংজ্ঞা তারা এভাবেই নিরুপণ করে যে, বেদবিরোধী মাত্রই নাস্তিক। কাজেই জৈন ও বৌদ্ধরাও নাস্তিক। অতঃপর উভয় ধর্মীয়দের নিরীশ্বরবাদী প্রবণতা প্রমাণ করার চেষ্টা চলে”। (বাংলাদেশে ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮)
মওলানা আবুল কালাম আযাদ দেখিয়েছেন যে, বুদ্ধ কখনো নিজেকে ভগবাদ দাবি করেননি। অশোকের যুগ পর্যন্ত বুদ্ধ-মূর্তির প্রচলনও কোথাও ছিল না। প্রতিমা পূজাকে সত্যের পথে এক বিরাট বাধা গণ্য করে সেই অজস্র খোদার খপ্পর থেকে বুদ্ধ মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি ব্রাহ্মণ্য খোদাকে অস্বীকার করে দিব্যজ্ঞানলাভ ও সত্য-সাধনায় মুক্তি নিহিত বলে ঘোষণা করেছিলেন।
বাংলায় দ্রাবিড়দের প্রতিরোধের ফলে দীর্ঘ দিন আর্য-প্রভাব ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়। এরপর খ্রিস্টীয় চার ও পাঁচ শতকে গুপ্ত শাসনে আর্য ধর্ম, আর্য ভাষা ও আর্য সংস্কৃতি বাংলাদেশে প্রত্যক্ষভাবে শিকড় গাড়ে। তৃতীয় ও চতুর্থ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে আর্য বৈদিক হিন্দু ধর্মের কিছুই প্রসার হয়নি। ষষ্ঠ শতকের আগে বঙ্গ বা বাংলার পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ঢুকতেই পারেনি। উত্তর-পূর্ববাংলায় ষষ্ঠ শতকের গোড়াতেই ব্রাহ্মণ্য সমাজ গড়ে ওঠে। পঞ্চম ও অষ্টম শতকের মধ্যে ব্যক্তি ও জায়াগার সংস্কৃতি নাম পাওয়া যায়। তা থেকে ড. নীহাররঞ্জন রায় অনুমান করেন যে, তখন বাংলার আর্যয়করণ দ্রুত এগিয়ে চলছিল। বাঙালি সমাজ উত্তর ভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত হচ্ছিল। অযোধ্যাবাসী ভিণ প্রদেশী বাহ্মণ, শর্মা বা স্বামী, বন্দ্য, চট্ট, ভট্ট, গাঙি নামে ব্রাহ্মণেরা জেঁকে বসেছিলঃ
“বাংলাদেশের নানা জায়গায় ব্রাহ্মণেরা এসে স্থায়ী বাসিন্দা হতে লাগলেন, এরা কেই ঋগ্বেদীয়, কেই বাজসনেয়ী, কেউ শাখাব্যয়ী, যাজুর্বেদীয়, কেই বা সামবেদীয়, কারও গোত্র কান্ব বা ভার্গব, বা কাশ্বপ, কারও ভরদ্বাজ বা অগস্ত্য বা বাৎসা বা কৌন্ডিন্য। এমনি করে ষষ্ঠ শতকে আর্যদের বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ বাংলার পূর্বতম প্রান্তে গিয়ে পৌঁছল”। (ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ঃ বাঙালির ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃষ্ঠা ১৩২)
সাত শতকের একেবারে শুরুতে গুপ্ত রাজাদের মহাসামন্ত ব্রাহ্মণ্য-শৈবধর্মের অনুসারী শশাংক রাঢ়ের রাজা হয়ে পুন্ড্রবর্ধন অধিকার করেছিলেন। মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করে তিনি বৌদ্ধ নির্মূলের নিষ্ঠুর অভিযান পরিচালনা করেন। রাজা শশাংক গয়ায় বোধিবৃক্ষ ছেদন করেন। তিনি আদেশ জারি করেনঃ
“সেতুবন্ধ হইতে হিমালয় পর্যন্ত যেখানে যত বৌদ্ধ আছে, তাহাদের বুদ্ধ হইতে বালক পর্যন্ত যে না হত্যা করিবে, সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে”। (রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ, পৃষ্ঠা ১২৪)
সাত শতকের শেষার্ধ থেকে আট শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত গোর বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ‘মাৎসান্যায় যুগ’। এ যুগে জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রামের শিথিলতার সুযোগে আর্য-ব্রাহ্মণেরা তাদের তৎপরতা আরো জোরদার করে। এ সময় বৌদ্ধ ধর্মের সাংস্কৃতিক আদর্শের ওপর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। মাৎস্যন্যায়ের এ অন্ধকার যুগেই এদেশে সংস্কৃত ভাষাও মাথা তোলে।
পাল আমলঃ বৌদ্ধ সংস্কৃতির আয়ূ বৃদ্ধি
দীর্ঘ এক শতাব্দীর মাৎস্যন্যায় যুগের অবসান ঘটিয়ে আট শতকের মধ্যভাগে গরিষ্ঠ জনমতের প্রতিফলনের ভিত্তিতে গৌড়-বঙ্গ-বিহারে বৌদ্ধ মতাবলম্বী পাল শাসনের সূচনা হয়। পাল শাসনের চারশ’ বছর ছিল এদেশের মানুষের গৌরব পুনরুদ্ধার, আত্ম-আবিষ্কার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ। এ আমলে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার ও সংঘারাম ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র। কয়েকটি ছাড়া সকল মহাবিহার ছিল বাংলাদেশে। দশ শতকের শেষভাগের জেষ্ঠ্যজেতাবীর বাড়ি ছিল উত্তর বঙ্গে। তার ছাত্র বিক্রমপুরের অতীশ দীপংকর শ্রজ্ঞান (৯৮০-১০৩৫) জ্ঞানরাজ্যের এক বিশ্ববিশ্রত নাম। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ্য শীলভদ্রও ছিলেন বাংলাদেমের অধিবাসী। তিনি ছিলেন হিউয়েন সাঙ-এর শিক্ষক। জনগণের মুখের ভাষার মর্যদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এ যুগের আরেক গৌরব। এ যুগে ছিল বাংলা ভাষার সৃজ্যমান কাল।
বাংলার পাল-রাজত্ব চারশ’ বছর স্থায়ী হয়। গৌড়-বঙ্গে পাল শাসন চলাকালে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে সমসাময়িক আর্য-ব্রহ্মণ্য শক্তিপুঞ্জ সুলতান মাহমুদের হামলায় বিব্রত ও বিপর্যস্ত ছিল। ফলে পাল শাসন তার ভৌগোলিক সীমান্তে দীর্ঘদিন নিরুপদ্রব থাকে। আট শতক থেকে এগারো শতক পর্যন্ত পাল শাসনে বাংলায় বৌর্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। বাংলা ও বিহার ছাড়িয়ে এ ধর্ম এ সময় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা অর্জন করে। পূর্ব ভারত ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। ফলে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের পরমায়ূ আরো চার-পাঁচশ বছর বৃদ্ধি পায়।
পাল আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বৌদ্ধ-ধর্ম-সংস্কৃতির সাথে বৈদিক ধর্ম-সংস্কৃতির মিল-সমন্বয়ের স্লোগান দেয়। বহিঃসীমান্তে তাদের মিত্ররা সামরিকভাবে সুবিধা করতে না পারলেও ব্রাহ্মণদের এই চতুর কৌশল বিশেষ ফলদায়ক হয়েছিল। ড. নীহাররঞ্জন রায় তারই বিবরণ দিয়ে জানাচ্ছেনঃ
“পাল রাজাদের অনেকেই ব্রাহ্মণ রাজ-পরিবারের মেয়ে বিয়ে করছিলেন। ফলে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল”। (বাঙালির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৩৯)
এ সময় পাল রাজারা অনেকেই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ্য মূর্তি আর তাদের মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছিলেন। তাদের চিন্তা-চেতনা ও ক্রিয়াকর্মে নিজ সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য মুছে গিয়ে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব স্পষ্ঠ হয়ে ফুটে উঠেছিল। বিশেষত দশ শতক থেকে বৌদ্ধ ধর্মে পূজাচারের প্রভাব দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় হলো, পাল-পূর্ব যুগের বৌদ্ধ মূর্তি বিশেষ পাওয়া যায় না। যা কিছু পাওয়া যায় নয় শতক থেকে এগারো শতকের মধ্যেকার। এই সমন্বয় ছিল এক তরফা। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ছাঁচেই গড়ে উঠেছিল সবকিছু। নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়ঃ
“এই মিল-সমন্বয় সত্ত্বেও বৌদ্ধ ধর্ম তার দেবায়তন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুক্ষগত হয়ে পড়ছিল।…… বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাহ্য ব্যবধান ঘুচে যাওয়ায় লোকের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকর্ষণ কমে এসেছিল”। (বাঙালির ইতিহাস, ১৫১)
তথাকথিত এই মিল-সমন্বয়ের আদর্শ বাংলাদেশের জনগণের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের খোল-নলচে পাল্টে দিচ্ছিল, তাদের জাতিসত্তাকে করে তুলেছিল অন্তঃসারশূন্য, আার রাষ্ট্রসত্তাকে করে তুলেছিল বিপন্ন। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা পাহারা দেওয়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতির সীমানা হেফাযত করতে না পারলে সে জাতির ভবিষ্যৎ পরিণতি কত মারাত্মক হতে পারে, তার প্রমাণ পাল শাসকেরা রেখে গেছেন।
সেন শাসনঃ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির একাধিপত্য
পাল-রাজত্বের অবসানের পর কর্ণাটদেশীয় চন্দ্র-বংশীয় ক্ষত্রিয় বর্ণের সেনরা বাংলাদেশ শাসন করে। দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে সামন্ত বিদ্রোহ ও ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগ নিয়ে সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন বারো শতকের শুরুতে রাঢ়-এর একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল দখল করে সামন্তরূপে জেঁকে বসেন। পাল বংশের শেষ রাজা রামপালের মৃত্যুর পর পাল-রাজ্যের গোলযোগ দেখা দেয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভগ্নাদশার এই সুযোগে হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন (মৃঃ ১১৫৮) এখানে প্রভুত্ব কায়েমের চেষ্ঠা করেন। তার রাজধানী ছিল বিজয়পুর। বঙ্গের বিক্রমপুরে ছিল তার দ্বিতীয় রাজধানী । শিব-এর পূজারী বিজয় সেন ও তার পুত্র বল্লাল সেন বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধারায় কুলীনপ্রথাভিত্তিক বর্ণশ্রমবাদী সমাজের ভিত রচনা করেন। তখনকার অবস্থা ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেনঃ
“সেন শাসনামলে দেখতে দেখতে যাগযজ্ঞের ধুম পড়ে গেল। নদ-নদীর ঘাটে-ঘাটে শোনা গেল বিচিত্র পুণ্য-স্নানার্থীর মন্ত্র-গুঞ্জরণ, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পূজা, বিভিন্ন পৌরাণিক ব্রতের অনুষ্ঠান, জনগণের দৈনন্দিন কাজর্ম, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, শ্রাদ্ধ, আহার-বিহার, বিভিন্ন বর্ণের নানা স্তর-উপস্তর বিভাগের সীমা-উপসীমা- এক কথায় সমস্ত রকম সমাজ-কর্মের রীতি-পদ্ধতি ব্রাহ্মণ্য নিয়ম অনুযায়ী বেঁধে দেওয়া হলো। এক বর্ণ, এক ধর্ম ও এক সমাজাদর্শের একাধিপত্যই সেন-বর্মন যুগের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। সে সমাজাদর্শ পৌরণিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের আদর্শ। সে আদর্শই হলো সমাজের মাপকাঠি। রাষ্ট্রের মাথায় রাজা, তার প্রধান খুঁটি ব্রাহ্মণেরা। কাজেই মূর্তিতে, মন্দিরে, রাজকীয় লিপিমালায়, স্মৃতি-ব্যবহারে ও ধর্মশাস্ত্রে সমস্ত রকম উপায়ে এই আদর্শ ও মাপকাঠির ঢাক পিটানো হতে লাগল। রাষ্ট্রের ইচ্ছায় ও নির্দেশে সর্বময় ব্রাহ্মণ্য একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো”। (ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ঃ বাঙালির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭)
সেন আমলে বর্ণাশ্রম প্রথা পুরোপুরি চালু হলো। উৎপত্তি হলো ছত্রিশ জাতের। যারা উৎপাদনের সাথে যত বেশি সম্পর্কযুক্ত, তাদের স্থান হলো সমাজে ততো নীচুস্তরে। যারা যতো বেশি উৎপাদন-বিমুখ, অন্যের শ্রমের ওপর যত বেশি নির্ভরশীল, যত বেশি পরভোজী ও পরাশ্রয়ী, সমাজে তাদের মার্যাদা হলো তত উপরে। ব্রাহ্মণ্য বর্ণ বিন্যাসের এই ছিল বৈশিষ্ট্য। এভাবে সেন-বর্মন শাসিত বাংলাদেশে একটি সর্বভুক পরগাছাশ্রেণীর স্বৈরাচার কায়েম হয়।
জাতিসত্তা বিনাশের অভিযান
পাল আমলে সাংস্কৃতিক আধিপত্য কায়েমের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ব্রাহ্মণেরা তথাকথিত মিল-সমন্বয়ের কৌশল গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সেন-বর্মন পর্বে ব্রাহ্মণ্য সমাজ তথাকথিত সমন্বয়ের মুখোশ আর রাখল না। তারা স্বমূর্তিতে আগ্রাসনের দাঁত-নখ ব্যাদান করে রাজপথ আগলে দাঁড়াল। পাল আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি যে উদারতা দেখান হয়েছিল, তার বদলা হিসেবে ব্রাহ্মণবাদী সেনরা বৌদ্ধ ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার বিরুদ্ধে পরিচালনা করল নিষ্ঠুর নির্মূল অভিযান। সে নিষ্ঠুরতার ব্যাপ্তি সম্পর্কে বর্তমান আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের একটি উদ্ধৃতি দেওয়াই যথেষ্ট মনে করি। ‘ডিসকভারিজ অব লিভিং বুদ্ধইজম ইন বেঙ্গল’ গ্রন্হের বরাত দিয়ে তিনি লিখেছেনঃ
“যে জনপদে (পূর্ববঙ্গ) এক কোটির অধিক বৌদ্ধ এবং ১৫৫০ ঘর ভিক্ষু বাস করিত, সেখানে একখানি বৌদ্ধ গ্রন্হ ত্রিশ বছরের চেষ্টায় পাওয়া যায় নাই। যে পূর্ব ভারত বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান লীলাকেন্দ্র ছিল, তথায় বৌদ্ধ ধর্মের যে অস্তিত্ব ছিল, তাহাও ইউরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিক চেষ্টায় অধুনা আবিস্কৃত হইতেছে”। (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান, পৃষ্ঠা ১১-১২)
ভারতে তথা বাংলাদেশে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অবলুপ্তি প্রসঙ্গে বিশ্বেশ্বর চৌধুরী লিখেছেনঃ
“ভারতের মাটি ও আবহাওয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতা মৌসুমী ফুলের মতই অবলুপ্ত হয়নি। এই পতন ও এই অবলুপ্তি অবশ্যই স্বাভাবিক ঘটনা নয়- সম্পর্ণ অস্বাভাবিক। ভারত-ভূমিতে বৌদ্ধ ধর্ম ও সমাজের অবলুপ্তি এর আয়ুষ্কালের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি নয়, এটা কঠোর হস্তের একটা নির্মম হত্যাকাণ্ড………..। ……….. আমি শুধ বৌদ্ধ স্তূপ, মঠ, বিহার ও বুদ্ধমূর্তির ধ্বংসস্তূপগুলোর প্রতি অঙ্গুলি সংকেত দ্বারা উল্লেখ করব যে, ঐ সকল ধ্বংসস্তূপই বৌদ্ধ ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা, শিল্প ও সংস্কৃতি গঠনের সাধনা ও সিদ্ধি এবং বিরুদ্ শক্তি কিরূপ নির্মম হস্তে সে সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে সমাহিত করেছে তারই জ্বলন্ত প্রমাণ- জীবন্ত স্বাক্ষর”। (টেকনাফ থেকে খাইবার, পৃষ্ঠা ২১)
সেন-বর্মন শাসনামলে ব্রাহ্মণ্যবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুখে বৌদ্ধ জাতিসত্তার সাথে এ এলাকার জনগণের মুখের ভাষার অস্তিত্বের সংকটও সৃষ্টি হয়েছিল। সেই চরম দুর্গতির বিবরণ দিয়ে অধ্যাপক দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেনঃ
“পাল বংশের পরে এতদ্দেশে সেন বংশের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের চিন্তা অতিশয় ব্যাপক হইয়া ওঠে ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবাহ বিশুষ্ক হইয়া পড়ে। সেন বংশের রাজারা সবাই ব্রাহ্মণ্যধর্মী, তাহাদের রাজত্বকালে বহু ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করে ও অধিকাংশ প্রজাবৃন্দ তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এভাবে রাজ ও রাষ্ট্র উভয়ই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিরূপ হইলে বাংলার বৌদ্ধরা স্বদেশ ছাড়িয়া নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি পার্বত্য প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বাংগালার বৌদ্ধ সাধক কবিদের দ্বারা সদ্যজাত বাংগালা ভাষায় রচিত গ্রন্হগুলিও তাহাদের সঙ্গে বাংগালার বাহিরে চলিয়া যায়। তাই আদি যুগের বাংগালা গ্রন্হ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য”।
(প্রাচীন বাংগালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৯-১০)
সে আমলের বাংলা ভাষার কিছু নমুনা ১৯০৭ সালে ড, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন। চর্যাপদ নামে পরিচিত এই চারটি পুঁথি প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নিদর্শন শুধু নয়; আমাদের পূর্বপুরুষদের আর্য-আগ্রাসনবিরোধী সংগ্রামের কাহিনী এবং তাদের রুদ্ধ হাহাকার এসব প্রাচীন পুঁথির পাতায় কান পাতলে শোনা যায়।
প্রতিরোধ সংগ্রামে নতুন ধারা
সেন-বর্মন যুগের ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন এবং অর্থনৈতিক শোষণে দেশবাসীর জীবন যখন বিপন্ন, সে সময় মজলুম জনগণের পক্ষের শক্তির হিসেবে তাদের পাশে এসে দাঁড়ান ইসলাম প্রচারক আলেক, সূফী ও মুজাহিদগণ। বাংলাদেশে রাজা শশাংকের সময় থেকেই ইসলাম প্রচারকদের আগমনের সূচনা হয়। এরপর মাৎস্যন্যায় যুগের ঘন অন্ধকার ভেদ করে ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী গুঞ্জরিত হচ্ছিল দেশের নানা জায়গায়। ইসলাম প্রচারকগণ নিপীড়িত জনগণকে সংগঠিত করে রুখে দাঁড়ান বিক্রমপুরে, পুন্ড্রবর্ধনে, রামপুর বোয়ালিয়া বা রাজশাহীতে।
দশ ও এগারো শতক থেকে অসহায় দলিত মানুষের কানে ইসলামের মুক্তিবাণী গুঞ্জরিত হচ্ছিল গৌড় থেকে চট্টগ্রাম এবং সিলেট থেকে মঙ্গলকোট পর্যন্ত। ব্রাহ্মণ্যবাদ মানুষে মানুষে যে কৃত্রিম বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল, ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী ছিল তার বিরুদ্ধে প্রবল দ্রোহাত্মক উচ্চারণ।
দ্বাদশ শতকের শেষ নাগাদ বাংলার প্রায় প্রতিটি বিখ্যাত শহরে-বন্দরে এবং দেশের অভ্যন্তরভাগে বিখ্যাত গ্রামে সত্য ও মিথ্যা, হক ও বাতিল এবং ইসলাম ও কুফরের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। এই দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্বে সাধারণ মানুষের কাছে সত্যের চেহারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। গাঙ্গেয় উত্যকার অভ্যন্তরে এক নীরব বিপ্লবের ধারা এগিয়ে চলে। আর্যদের বৈদিক ও পৌরণিক ধর্মের বিরুদ্ধে বাংলার অধিবাসীরা হাজার বছর ধরে যে প্রতিরোধ গড়ে আসছিল, ইসলামের দ্রোহাত্মক বানী তাদের সে প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলল।
একেকজন ইসলাম প্রচারক জনগণের কাছে আবির্ভূত হন তাদের মুক্তি সংগ্রামের মহানায়করূপে। প্রচারকদের গড়ে তোলা মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাগুলো নির্যাতিতের আশ্রয়স্থল, অভুক্তের লঙ্গরখানা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মতবিনিময় ও চাহিদা পূরণের কেন্দ্র এবং মুক্তি সংগ্রামের দুর্গ হিসেবে পরিচিত হয়।
বাঙালিয় ইতিহাস-নিহার রঞ্জন রায়
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস- নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি
বঙ্গে জাতীয় ইতিহাস- ব্যোমকেশ মোস্তাফি
‘এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া’ -মাইকেল এডওয়ার্ডট
বাঙালির ইতিহাস- মোহাম্মদ হান্নান
বাঙালি জাতি বাঙালি মুসলমান ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ -সৈয়দ আবুল মকসুদ
বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস-আব্দুল করিম
আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা-মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান
বাঙালাদেশের ইতিহাস চর্চা-বদরুদ্দীন উমর
লেখ-আল-আমিন শেখ
বিশ্ব ইতিহাস ও ইসলামের স্বর্ণযুগ